.png)
—রসময় উপমার এক রম্য আলাপ–আনালজিক্যাল স্টোরিটেলিং ফিচার সিরিজ | অধিকারপত্র স্টাইল|
প্লেটোর 'গুহার উপমা' কি আজও বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিক? এরিস্টটলের নৈতিকতার 'আন্তোষ্টিক্রিয়া' কেন ঘটল? রম্য সাহিত্য ও গভীর দর্শনের মিশেলে এই ফিচার স্টোরি উন্মোচন করছে রাজনীতি, শিক্ষা ও নৈতিকতার এক দার্শনিক অসামঞ্জস্য। পড়ুন এবং ভাবুন: আমরা কি সত্যিই আলো দেখছি, নাকি Wi-Fi যুক্ত গুহার মায়ায় ভার্চুয়াল জগতে আবদ্ধ হয়ে অলীক স্বপ্নে রঙিন আলোর ফানুস উড়াচ্ছি?
প্রথম পর্ব: ঢাকার চায়ের দোকানে প্লেটোর আগমন
শিষ্য এরিস্টটলের নির্বাক প্রত্যাবর্তনের পর, স্বয়ং গুরু প্লেটো পা রাখলেন ঢাকায়। ঢাকার একটি পুরনো চায়ের দোকানে— যেখানে দেশ, রাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা আর আদর্শের বিশাল বিশাল আলোচনা চা পাতার ধোঁয়ার সাথে মেশে—সেখানে ঘটল এক মহাজাগতিক ঘটনা। হঠাৎ করেই গ্রিস থেকে টাইম-ট্রাভেল করে আসা প্লেটো এসে বসলেন চায়ের টেবিলে! কাঁধে তাঁর সেই কালজয়ী ক্লোক, হাতে দার্শনিক ভঙ্গি আর চোখে হাজার বছরের বিস্ময়।
“এ কোন নগররাষ্ট্র?”
“স্যার, এটা ঢাকা। পাঁচ হাজার বছরের আপগ্রেডেড সংস্করণ।”
প্লেটো ভুরু কুঁচকে তাকালেন। “তোমাদের রাষ্ট্রে কি ‘দর্শনসম্রাট’ (Philosopher King বা PR) আছে? নাকি সবাই শুধু আলো দেখে অন্ধকারকে ভুলে গেছে?”
চায়ের দোকানের মালিক তড়াক করে বলল— “কি যে বলেন মুরুব্বি! আসলে এখানে আলো-অন্ধকার দুটোই আছে। তবে অনেকে আলোয় দাঁড়িয়ে থেকেও ছায়াকে সত্যি ধরে।”
প্লেটো বুঝলেন, এই নগররাষ্ট্রে তাঁর 'Cave Allegory' (গুহার উপমা) আজও জ্বলন্ত সত্য।
দ্বিতীয় পর্ব: গুহার উপমা ও বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি— ছায়ার সঙ্গে প্রেম
প্লেটো বলেছিলেন— মানুষ অনেকসময় বাস্তবতা দেখে না; দেয়ালের ছায়াকেই বাস্তব মনে করে। আধুনিক বাংলাদেশে সেই গুহার তুলনা টানলে কেমন হয়?
১. তথ্যের গুহা— সোশ্যাল মিডিয়ার দেয়ালে হাঁসফাঁস: প্লেটোর সময় ছায়া পড়ত পাথরের দেয়ালে, আর আজ সেই ছায়া পড়ে কম্পিউটার বা স্মার্ট-ফোনের স্ক্রিনে— এ যেনো ফেসবুকের নিউজফিড, ভাইরাল ভিডিও, টিকটকের ‘দর্শন’—সব মিলিয়ে সত্যি–মিথ্যার এক জটিল থিয়েটার। এখানে যে যত জোরে কথা বলে, সেই তত বেশি Reality Show Philosopher।
সত্যিকারের চিন্তাবিদরা এখনো গুহার মুখে দাঁড়িয়ে বলে—“ভাই, আলোটা দেখুন!” কিন্তু মানুষ উত্তর দেয়—“একটু দাঁড়ান, আগে লাইভটা শেষ করি!”
২. রাজনীতির গুহা— আদর্শের বদলে ছায়ার লড়াই: প্লেটো চেয়েছিলেন, রাষ্ট্র চালাবেন দার্শনিকেরা—যারা সত্যকে ভালোবাসে, ক্ষমতাকে নয়। বাংলাদেশে? ক্ষমতার ছায়া এত লম্বা যে আদর্শ কোথায় দাঁড়িয়েছে, তাইই বোঝা যায় না। যে ছায়া বড়, সেই প্রভাবশালী। যে ছায়া তীক্ষ্ণ, সে ‘বিরোধী’। আর যার ছায়াই নেই, সে ‘পরামর্শদাতা’। প্লেটো একথা শুনে হাঁটুতে হাত দিয়ে বসলেন—“তোমরা ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করো কেন? আলোর দিকে ঘুরে দাঁড়াও, ছেলে!” চায়ের দোকানের ছেলেটি বলল—“স্যার, আলো ধরতে গেলে আগে লোডশেডিং বন্ধ করতে হবে।” প্লেটো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
৩. শিক্ষার গুহা—মুখস্থ জ্ঞান বনাম চিন্তার আলো: প্লেটোর একাডেমি ছিল চিন্তার মুক্তভূমি। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষা—অনেক ভালো দিক থাকলেও—যেন এখনো বইয়ের ‘ছায়া’য় আবদ্ধ। প্লেটো প্রশ্ন করলেন—“চিন্তা করলে মার্কস কমে যায় নাকি?” জবাব এলো—“চিন্তা না করলে মানুষই কমে যায়।”
৪. নৈতিকতার গুহা—উন্নয়নের আলো, নীতির অন্ধকার: অর্থনৈতিক উন্নয়ন চমৎকার আলো দিচ্ছে। কিন্তু সেই আলোয়ও মাঝে মাঝে দেখা যায় ছায়া—দুর্নীতি, বৈষম্য, অন্যায়ের কুয়াশা। ঢাকার রাস্তায় নালার পাশে মোটরবাইক উল্টানো দেখে প্লেটো এক বাক্য বললেন, “এই নগররাষ্ট্রে Drainage Philosophy অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।” চায়ের দোকানের ভিড় হো হো করে হেসে উঠল।
তৃতীয় পর্ব: এরিস্টটলের দীর্ঘশ্বাস ও ‘সিন্ডিকেটলজিক’ এর আবির্ভাব
গুরু প্লেটোর ঢাকায় আসার পূর্বেই এক অসামান্য ঘটনার জন্ম হয়েছিল। এরিস্টটল তাঁর মৃত্যুর ২,৩৪৭ বছর পর বাংলাদেশে নেমে এসেছিলেন। নেমেই তিনি হতবাক! দেখলেন, তাঁর ছয় অমরবাণী—যা ছাত্রদের জীবন ও নৈতিকতার পথ দেখানোর জন্য রেখেছিলেন—সেগুলোরই যেন ‘আন্তোষ্টিক্রিয়া’ চলছে। একটি ব্যানারে লেখা— “সততা ভালো, তবে বাস্তবতার সাথে মানায় না।"
আরেকটিতে—
“গুণ (Virtue) = প্রেজেন্টেশন + PR + প্রভাবশালী সম্পর্ক।”
এরিস্টটল হাহাকার করে বললেন— “হায়! আমার নৈতিকতার মাঝপথে বাংলাদেশ এসে দাঁড়িয়েছে!” তিনি আকাশপানে তাকিয়ে মনে মনে বললেন—“এ দেশে যেন Syllogism (যুক্তিবিদ্যা) চলে না; চলে শুধুই ‘সিন্ডিকেটলজিক’।”
মন ভারাক্রান্ত হয়ে তিনি ফিরে গেলেন স্বর্গে। সেখানে প্রথমেই দেখা পেলেন তাঁর শ্রদ্ধেয় গুরু প্লেটোর।
চতুর্থ পর্ব: গুরু–শিষ্যের স্বর্গীয় আলাপ: আজব দেশের গল্প
প্লেটো বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন— “এই কেমন মুখ করে এসেছো এরিস্টটল?”
এরিস্টটল ধীরে ধীরে বললেন— “গুরু, আমি এমন দেশ দেখেছি যেখানে তোমার দর্শন আর আমার নৈতিকতা দুটোই ওলট-পালট। সেখানে থিওরি চলে না, নৈতিকতা চললে তাকে বলা হয় ‘দুর্বলতা’, আর যুক্তি দিলে বলে—‘ভাই, বাস্তবতা দেখেন’।”
প্লেটো অবাক হয়ে বললেন— “এমনও হয়? তাহলে আমাকেই দেখে আসতে হবে!”
এরিস্টটল সাবধান করলেন— “গুরু, ওখানে কেউ আলো দেখতে চায় না। ছায়াকেই সত্যি ধরে। তবুও যদি যেতে চান—পকেটে কিছু ধৈর্য আর রসিকতা নিয়ে যাবেন।”
প্লেটো হাসলেন— “জ্ঞান যেখানে থাকে, সেখানে ধৈর্য থাকে। হাসিও থাকে।” এবং যথারীতি তিনি চলে এলেন বাংলাদেশে।
পঞ্চম পর্ব: প্লেটোর চোখে ধরা পড়া ‘দার্শনিক অসামঞ্জস্য’
চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসেই প্লেটো বুঝে গেলেন— এ দেশ দার্শনিকভাবে অদ্ভুত।
- ‘গণতন্ত্র’ বনাম ‘গোষ্ঠীক্রতন্ত্র’: প্লেটো দেখলেন— অনেকে যুক্তি নয়, পরিচয় দেখে সিদ্ধান্ত নেয়। এক পক্ষ ভুল করলেও সমর্থন করে, অন্য পক্ষ সঠিক করলেও সমর্থন পায় না। প্লেটো বললেন— “একে গণতন্ত্র নয়, ‘গোষ্ঠীক্রতন্ত্র’ বলা যায়।”
- ‘দার্শনিক শাসক’ নয়—জনপ্রিয়তার PR: প্লেটো বলেছিলেন, শাসক হবে যার জ্ঞান, নৈতিকতা আর সত্যের প্রতি ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু বাংলাদেশে শাসকের যোগ্যতা = PR + প্রভাব + প্রচারণা। তিনি আক্ষেপ করলেন—“জ্ঞানী নয়, জনপ্রিয়জনকেই এখানে Philosopher King ভাবা হয়!”
- ‘ন্যায়’ এখানে বিচারকের হাতে নয়—ফাইল ও ধৈর্যের উপর: বিচার পেতে অনেক ক্ষেত্রে ফাইলের গতির উপর নির্ভর করতে হয়। তিনি অবাক হয়ে বললেন— “ন্যায় যদি অপেক্ষায় থাকে, রাষ্ট্রের আত্মা ক্লান্ত হয়ে পড়ে।”
- ‘শিক্ষা’ জ্ঞানের জন্য নয়—সার্টিফিকেট সংগ্রহের দৌড়: প্লেটোর একাডেমির মূলনীতি ছিল: “শিক্ষাই চরিত্র গঠন করে।” এখানে এসে তিনি দেখলেন— অনেক ছাত্র জ্ঞান নয়, শুধুই পরীক্ষার মার্কের পিছনে দৌড়াচ্ছে। চিন্তা করার চেয়ে নোট মুখস্থ করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এক বালকের কথা শুনে তিনি হতবাক— “স্যার, চিন্তা করলে তো ভুল হয়ে যায়!”
- ‘সত্য’ বেঁচে থাকে, কিন্তু ‘সত্য-বলিয়েরা’ বিপদে: সত্য বললে অনেক সময় ‘ঝামেলা’ হয়। তাই মানুষ ‘পরোক্ষ সত্য’ বা ‘সাবধানে সত্য’ বলতে শিখেছে। তিনি বললেন— “যেখানে সত্য বলার জন্য ভয়ের প্রয়োজন হয়, সেখানে গুহা এখনও ভাঙেনি।”
আজকের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দার্শনিক বিশ্লেষণ
তাহলে নিচে প্লেটোর দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চায়ের দোকানের কথোপকথনের’ ঢঙে আরও সূক্ষ্ম ও গভীর ‘দার্শনিক বিশ্লেষণ নিচে তুলে ধরা হলো:
প্লেটোর অপ্রকাশিত মন্তব্য: আধুনিক ঢাকা নিয়ে আরও ছয়টি সংব্যাখ্যান
চায়ের টেবিলে বসে প্লেটো এবার কাপ হাতে নিলেন, চোখ বন্ধ করে যেন প্রাচীন এথেন্সের ধুলো ঝেড়ে ফেললেন।
১. আবেগ ও যুক্তির দড়ি টানাটানি (রাষ্ট্রের আত্মার বিশ্লেষণ): "রাষ্ট্রের আত্মা অসুস্থ হলে, ব্যক্তির মনও কষ্ট পায়।" প্লেটো এই কথা বলে চারপাশে তাকালেন।
- প্লেটোর মন্তব্য: "আমি তোমাদের নগরবাসীদের মধ্যে তিন শ্রেণির আত্মাকে দেখছি—ক্ষুধা (Appetite), সাহস/আবেগ (Spirit), এবং যুক্তি (Reason)। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এখানে 'ক্ষুধা' (অর্থাৎ ব্যক্তিগত লোভ ও ভোগ) শাসক হয়েছে, 'সাহস' (বীরত্ব ও ন্যায়) কেবল নিজেদের গোষ্ঠীর জন্য কাজ করছে, আর 'যুক্তি' (জ্ঞান ও সত্য) রাস্তার কোণে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে! ন্যায়প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ছিল তিনটির মধ্যে ভারসাম্য। তোমাদের এখানে চলছে ‘তিন আত্মার মল্লযুদ্ধ’।"
- চায়ের দোকানের টিপ্পনী: "স্যার, এই মল্লযুদ্ধে বিজয়ীর জন্যই বাজারের সবচেয়ে দামি চা এবং সবচেয়ে দামি বাড়ির টিকিট বরাদ্দ থাকে।"
২. সম্পদের প্রতি অনুরাগ বনাম রাষ্ট্রের প্রতি অনুরাগ: প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে শাসক শ্রেণির জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক বন্ধন সীমিত করার কথা বলেছিলেন, যেন তারা পক্ষপাতিত্বমুক্ত থাকতে পারেন।
- প্লেটোর মন্তব্য: "আমি দেখি, যে রক্ষক (Guardian) হওয়ার কথা, সেই সবচেয়ে বেশি সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত। যাদের রাষ্ট্রের প্রতি অনুরাগী হওয়ার কথা, তারা এখন কেবল 'পারিবারিক সম্পত্তির অনুরাগী'। যখন শাসক ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়ানোকেই জীবনের সর্বোচ্চ দর্শন বানায়, তখন সে আর রাষ্ট্রকে নয়, নিজের কোষাগারকে রক্ষা করে।"
- চায়ের দোকানের টিপ্পনী: "স্যার, একেই আমরা বলি 'আত্মউন্নয়ন'—ব্যক্তিগত উন্নতিই নাকি সমাজেরও উন্নতি।"
৩. কবি ও শিল্পের সেন্সরশিপের প্রাসঙ্গিকতা: প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে সমাজের উপর কাব্যের প্রখর আবেগময় প্রভাব দেখে কবিদের উপর সেন্সরশিপ আরোপ করতে চেয়েছিলেন, যেন তরুণদের আত্মা কলুষিত না হয়।
- প্লেটোর মন্তব্য: "তোমাদের এই যুগে কবিতা নেই, আছে 'ভাইরাল কনটেন্ট'। এই কনটেন্ট—যা আবেগ, মিথ্যা ও বিদ্বেষ ছড়ায়—এটাই তো আমার সেই ভয়! আমি কেবল চেয়েছিলাম শিল্পীরা যেন সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের কথাই তুলে ধরেন। কিন্তু এখন তো মিথ্যাই সবচেয়ে দ্রুত ভাইরাল হয়। এই যন্ত্রগুলো (সোশ্যাল মিডিয়া) কবিদের চেয়েও দ্রুত মানুষের আত্মাকে বিভ্রান্ত করছে। এখন শুধু কবি নয়, 'অ্যান্ড্রয়েড কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের'ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।"
- চায়ের দোকানের টিপ্পনী: "ঠিক বলেছেন স্যার, আমাদের প্রজন্ম এখন যুক্তির চেয়ে 'ট্রেন্ড'কেই বেশি ভালোবাসে।"
৪. গণতন্ত্রের দুর্বলতা (A Critique on Democracy): প্লেটো সবসময় গণতন্ত্রের সমালোচক ছিলেন, কারণ তাঁর মতে এটি অজ্ঞ ও অযোগ্যদের শাসনকে উৎসাহিত করতে পারে।
- প্লেটোর মন্তব্য: "তোমাদের এখানে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সেই স্বাধীনতার প্রয়োগ কি যুক্তিবান মানুষের হাতে? আমার ভয় ছিল—গণতন্ত্র যেন 'মূর্খ বা অযোগ্যের শাসনব্যবস্থা' না হয়ে ওঠে। যখন জনগণ যুক্তি না বুঝে স্রেফ নিজেদের ক্ষণস্থায়ী পছন্দ বা আবেগের ভিত্তিতে শাসক নির্বাচন করে, তখন তারা স্বাধীনতার নামে নিজেরাই নিজেদের জন্য শিকল তৈরি করে। এই নগররাষ্ট্রে নির্বাচনের জয়-পরাজয় কি প্রজ্ঞার জয়, নাকি সবচেয়ে ভালো স্লোগান দেওয়া অভিনেতার জয়?"
- চায়ের দোকানের টিপ্পনী: "স্যার, এটা এখন প্রজ্ঞার লড়াই না, এটা 'জনপ্রিয়তার শো', যেখানে অভিনেতা আর নেতার পার্থক্য কেবল পোশাকে।"
৫. প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার বিচ্যুতি (Platonic Love vs. Consumerism): প্লেটোনিক প্রেম ছিল দেহাতীত, জ্ঞান ও সুন্দরের প্রতি আত্মার পবিত্র অনুরাগ।
- প্লেটোর মন্তব্য: "আমি তোমাদের মাঝে প্রেম (Love) দেখেছি, কিন্তু তা যেন জ্ঞানের দিকে চালিত না হয়ে বস্তুগত ভোগের দিকে চালিত হচ্ছে। আমার 'প্লেটোনিক প্রেম' তত্ত্বের মূল কথা ছিল—সম্পদ, খ্যাতি বা দৈহিক সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী। চিরন্তন সত্যের প্রতিই আসল অনুরাগ থাকা উচিত। তোমাদের সমাজে মানুষ কেবল 'ভালো পণ্য' এবং 'ভালো উপাধি' পাওয়ার জন্য ছুটছে। এই 'ভোগের আকাঙ্ক্ষা'-ই তাদের আসল জ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।"
- চায়ের দোকানের টিপ্পনী: "আমরা এখন প্রেমকেও একটি 'ব্র্যান্ড' হিসেবে দেখি, স্যার। পুরনো হলে তা 'আনফলো' হয়ে যায়।"
৬. আইন ও নৈতিকতার দ্বন্দ্ব: প্লেটো তাঁর শেষ দিকের রচনা 'লজ' (Laws) গ্রন্থে আইনের গুরুত্ব স্বীকার করলেও, সবসময়ই নৈতিক নেতৃত্বকে আইনের ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন।
- প্লেটোর মন্তব্য: "তোমরা আইন তৈরি করছো, কিন্তু যদি আইনের রক্ষকরা নিজেরাই নৈতিকতা বিসর্জন দেয়, তবে হাজারো কঠোর আইনও রাষ্ট্রের আত্মাকে বাঁচাতে পারবে না। নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে কেউ নিজ স্বার্থ রক্ষা করলে সে জনসমর্থন হারিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হবে—এই সহজ সত্যটিও কেন এখানে এত কঠিন? আইন হল এক দুর্বল প্রজ্ঞা, যখন শাসকের নৈতিক বিবেক জাগ্রত থাকে না।"
- চায়ের দোকানের টিপ্পনী: "আমাদের এখানে কিছু আইন এমন, স্যার—যা শুধু গরিবদের জন্য তৈরি।"
দুই হাজার চারশত বছরের দূরদৃষ্টির স্বার্থকতা খুঁজে পেয়ে তৃপ্ত প্লেটো
স্বজনপ্রীতির ছায়ায় দাঁড়িয়ে প্লেটো দেখলেন— রাষ্ট্রের আত্মা কীভাবে নীরবে ক্ষয়ে যায়, প্লেটো দেখলেন আমাদের শাসকরা এখনোও তার নোটবুকেই আটকে আছেন।প্লেটো এদেশের শাসকদের খবরখবর জেনে গভীর নিশ্বাস ফেললেন। প্লেটো নিজের ভিতরে মেলাতে চাইলেন, “শাসকরা যে বলেছিলো যে দেশে নাকি সব ঠিকঠাক চলছে— কিন্তু ওয়াইফাই, ওয়ালেট আর ওয়াদা— তিনটাই সবচেয়ে অবিশ্বস্ত!” এরপরে প্লেটো নিজে নিজেই বললো, “সকালে ভেবেছিলাম দিনটা ভালো যাবে… দুপুরেই বুঝলাম—আমার ভাবনাও আমাকে নিয়ে মজা করছে।” এ নিয়ে প্লেটোর কোমল দার্শনিক হৃদয়ের ভেতরটায় যেন একটুখানি দুঃখের কুয়াশা জমল।
এবার বিড়বিড়িয়ে বললেন,“হায়! এ কেমন দেশ! শাসকদের স্বজনপ্রীতি এতো ভয়াবহ! বৈষম্যের এমন নির্মম চিত্র তো আমি আমার সময়েও দেখিনি!” এরপরে এক মুহূর্ত চুপ হয়ে রইলেন তিনি। মনে হলো, প্রাচীন এথেন্সের সেই দার্শনিক নীরবতা তাঁর ওপর ভর করেছে। কিন্তু খানিক পরেই আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠল— যেন কোথাও গভীর আনন্দের একটি আলোকরেখা হঠাৎ ছুটে এসেছে।
অতঃপর আকাশের দিকে চেয়ে তিনি দু’হাত তুললেন। এক অদ্ভুত পরিতৃপ্ত স্বরে বললেন, “সৃষ্টিকর্তা, আমি কৃতজ্ঞ! দুই হাজার চারশো বছর আগে যে দেশটিকে আমি কল্পনা করে ‘রিপাবলিক’-এ শাসকদের চরিত্র আঁকলাম—আজ মনে হচ্ছে সেই কল্পিত দেশটি ঠিক এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। তাই তো বলেছিলাম— শাসক হবেন ‘ফিলোসফার কিং’, কিন্তু তাঁদের কোনো সন্তান-পরিজন থাকবে না… কারণ স্বজনপ্রীতি একটি রাষ্ট্রের আত্মাকে বিষাক্ত করে দেয়।”
প্লেটোর কণ্ঠে তখন বিস্ময়, ব্যথা, আর অদ্ভুত এক উপলব্ধির মিশেল— যেন বহু শতাব্দী পরে এসে তিনি নিজের ভবিষ্যদ্বাণীকেই জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখলেন।
চূড়ান্ত প্লেটীয় আহ্বান: আমাদের গুহা ভাঙার সময়
প্লেটো অবশেষে বললেন, "তোমাদের দেশে সবকিছুই আছে—প্রাচুর্য, আবেগ, সম্ভাবনা। কিন্তু গুহা থেকে বেরোনোর পথে সবচেয়ে বড় বাধা বাইরের অন্ধকার নয়, বরং গুহার ভেতরের আরাম।"
প্লেটো বিদায় নেওয়ার সময় বললেন— “তোমরা ইতিমধ্যেই আলোর নাগাল পেয়েছো। এখন শুধু সাহস করে গুহা থেকে বেরিয়ে আসো।” চায়ের দাম পরিশোধ করতে গিয়ে তিনি আরও একটি রম্য বাক্য বললেন— “এ দেশে দর্শন শেখানো কঠিন নয়; শুধু গুহার Wi-Fi অফ করতে হবে।”
বাংলাদেশ প্রতিদিন বদলাচ্ছে—উন্নয়ন, ডিজিটালাইজেশন, চিন্তার পরিবর্তন। কিন্তু প্লেটোর শিক্ষা মনে করিয়ে দেয়— বাস্তবের আলো চিনতে না পারলে ছায়ার ভিড়ে সত্য হারিয়ে যায়। এই দেশের মানুষ আলোর পথে হাঁটতে জানে— প্রচেষ্টা আছে, ত্যাগ আছে, সংগ্রাম আছে। শুধু দরকার—দৃষ্টি বদলানোর।
চায়ের দোকান থেকে প্লেটো বিদায় নেওয়ার সময় বললেন— “তোমরা ইতিমধ্যেই আলোর নাগাল পেয়েছো। এখন শুধু সাহস করে গুহা থেকে বেরিয়ে আসো।” আর আমরা বললাম— “স্যার, আগামিকাল চায়ে আবার আসবেন!” তিনি হেসে বললেন—“নিশ্চয়ই। তবে এবার দার্শনিক ছাড় দিয়ে চা দিবে।”
প্লেটোর সেই দর্শনের গুহা আছে, আলোও আছে—আমাদের প্রয়োজন কেবল ‘দৃষ্টি’। প্লেটো অবশেষে বললেন— “বাংলাদেশ অসাধারণ সম্ভাবনাময়। এখানে আলো প্রচুর— কিন্তু মানুষ ছায়ার প্রেমে পড়েছে। যে দিন তারা আলোকে ভালোবাসতে শুরু করবে, সেদিন এ দেশ পৃথিবীর সবচেয়ে দার্শনিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।”
চায়ের দোকানের আমরা বললাম—“স্যার, আবার আসবেন!”
তিঁনি হেসে বললেন— “এসেই যাব। তোমাদের দেশে ছায়ারও এমন রঙিন রূপ—দেখলে মন ভরে যায়।নিশ্চয় গুরু সক্রেটিস পছন্দ করবেন! এবার ফিরে গিয়ে আমার গুরু সক্রেটিসকে তোমাদের কথা বলব, দেখি গুরু কি বলেন?”
চলে যাওয়ার জন্য চায়ের দোকানের বেঞ্চ থেকে উঠতে উঠতে একটু নি:শ্বাস ছেড়ে গম্ভীর গলায় দার্শনিক কিং-এর ঢং-এ বললেন, “গুরু সক্রেটিস, হয়তো তোমাদের এই দেশের রঙ্গ দেখতে উৎসাহীই হবেন। সবাই ভালো থাকবেন।নিজেদের স্টাইলে।” এই বলেই প্লেটো অদৃশ্য হয়ে গেলেন।
✍️ –অধ্যাপক ড. মাহবুব লিটু, উপদেষ্টা্ সম্পাদক, অধিকারপত্র (odhikarpatranews@gmail.com)


-2025-08-17-22-08-42_copy_640x360-2025-08-17-23-04-05.jpg)

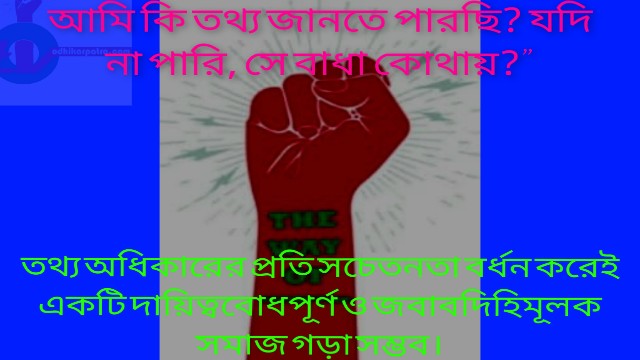

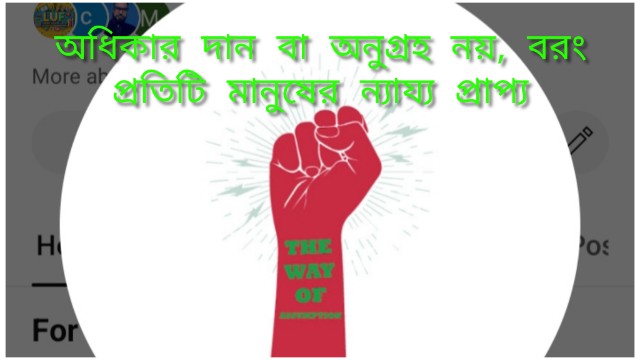

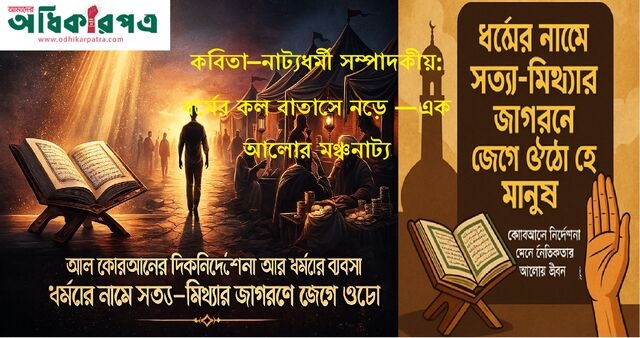


আপনার মূল্যবান মতামত দিন: